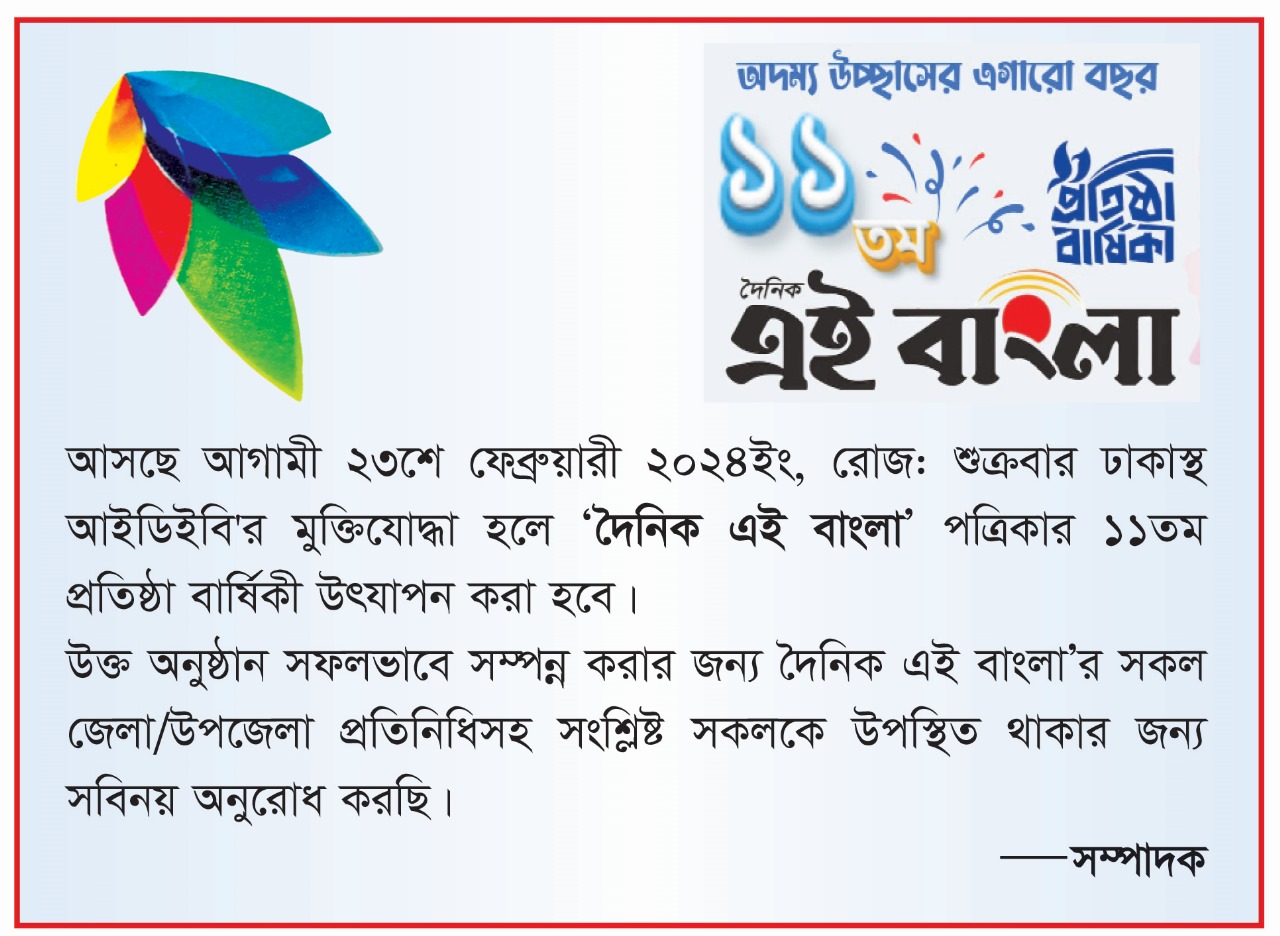এবার আপনাদের শোনাব বায়েজিদ বোস্তামির মতো আরেক সুফি-সাধকের কথা। তাঁর নাম মনসুর আল হাল্লাজ। আপনাদের মধ্যে যাঁরা সুফি তরিকার অনুসারী, তাঁরা নিশ্চয়ই মনসুর হাল্লাজের নাম শুনেছেন। সেদিন আমি রমেশ শীল আল মাইজভাণ্ডারির একটি গান শুনছিলাম। গানটির একটি পঙ্ক্তি এরকম :
‘মনসুরের কলবে থাকি আনল হক বলালি
শুলেতে তুলিয়া আবার জগৎকে দেখালি।’
পঙ্ক্তি দুটির মর্মার্থ আপনারা বুঝতে পারবেন মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর। বায়েজিদ বোস্তামি বলেছিলেন, ‘আমিই তুমি (আল্লাহ), তুমিই আমি।’ তাঁর মতো মনসুর হাল্লাজও বলেছিলেন, ‘আনাল হক।’ অর্থাৎ আমিই সত্য, আমিই আল্লাহ।
মনসুর হাল্লাজের পুরো নাম আবু আল-মুজিদ আল-হুসাইন ইবনে মনসুর আল-হাল্লাজ। তাঁর জন্ম ৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, পারস্যের ফার্স প্রদেশের মদিনা আল-বাইদা গ্রামে। তাঁর দাদা ছিলে জরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারী। মনসুরের বাবা আল-হাল্লাজও জরথুস্ত্রবাদী ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ধারণা করা হয়, তিনি তুলা বা পশম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আল হাল্লাজ অর্থ তুলাধূণী। আল হাল্লাজ তাঁর পুরো পরিবার নিয়ে ইরাকের ওয়াজিতের আরব কলোনিতে গিয়ে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানেই মনসুরের জন্ম।
ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবি ছিলেন মনসুর। মাত্র বারো বছর বয়সে ওয়াজিতের এক মাদ্রাসা থেকে তিনি কোরান মুখস্থ করেন। আঠারো বছর বয়সে তুস্তারে গিয়ে গ্রহণ করেন সুফি শাহল আল তুস্তারির শিষ্যত্ব। তুস্তারে দুই বছর থেকে চলে যান বাগদাদে এবং সেখান থেকে বসরায়। সুফি আমর মক্কীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রায় দুই বছর বসরায় অবস্থান করেন। এসময় বিয়ে করেন সুফি ইয়াকুব আল-আকতা কার্নাবাইয়ের কন্যা উম্মুল হুসনাইনকে। এই সংসারে তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম ছিল আহম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে মনসুর। বিয়ের কারণে গুরু আমর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
কারো কারো মতে, বিয়ের কারণে নয়, গুরু তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অন্য একটি কারণে। একবার গুরুর কোরান পাঠ শুনে মনসুর বলে ওঠেন, ‘আমিও ওই রকম লিখতে পারি।’ এই কথা বলার অপরাধে আমর তাঁকে পরিত্যাগ করেন। আবার কারো কারো মতে, আমরের সান্নিধ্যে থাকাকালীন মনসুর জ্ঞান-বিদ্যা ও সুফিতত্তে¡ আমরকে অতিক্রম করে ফেলেছিলেন। এ কারণেই আমরের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।
বসরা ছেড়ে মনসুর বাগদাদে গিয়ে বিখ্যাত সুফি জুনায়েদ বাগদাদির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুকাল বাগদাদির সঙ্গে থেকে যাত্রা করেন হেজাজের উদ্দেশে। তারপর হজের উদ্দেশ্যে চলে যান মক্কায়। কাবাঘরের দিকে মুখ করে তিনি এক বছর ধ্যান করেন। প্রতিদিন এক ব্যক্তি কয়েকটি রুটি ও এক পাত্র পানি দিয়ে যেত। মক্কা থেকে আবার ফিরে আসেন বাগদাদে। প্রায় বারো বছর পর বের হন দেশভ্রমণে। মধ্য এশিয়ার বহু এলাকা, চীন ও ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। তৈরি হয় তাঁর বহু শিষ্য। তাদের নিয়ে তিনি তিনবার হজ করেন। এরপর তিনি বসবাস শুরু করেন বাগদাদের আব্বাসিদ এলাকায়।
কথিত আছে, সুফি-সাধনায় রত অবস্থায় বিশ বৎসর ধরে একই জোব্বা পরিধান করে আসছিলেন মনসুর হাল্লাজ। জোব্বাটিতে ছিল তালি আর তালি। তিনি কখনো তাঁর পোষাক পরিবর্তনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। শিষ্যরা তাঁকে জোব্বা পরিবর্তনে রাজি করাতে পারেনি। একবার কয়েকজন শিষ্য মিলে জোর করে তাঁর জোব্বাটি খুলে তাঁকে নতুন একটি জোব্বা পরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। যখন তারা জোব্বাটি খুলল তখন দেখতে পেল একটা বড় বিচ্ছু জোব্বায় বাসা বেঁধে আছে। তখন মনসুর শিষ্যদের বলেন, এই বিচ্ছুটি আমার সঙ্গী। বন্ধুর মতো বিশটি বছর আমার জোব্বায় বসবাস করছে। বিচ্ছুসহ জোব্বাটি তিনি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। শিষ্যরা ফিরিয়ে দিল জোব্বাটি। আপনারা বলতে পারেন, এ কেমন কথা! বিশ বছর বিচ্ছুর সঙ্গে বসবাস! ইসলামে তো বলা হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। হ্যাঁ, আপনারা বলতেই পারেন। তবে জেনে রাখবেন, সুফিদেরকে ইসলামি বিধি-বিধানের গণ্ডিতে আটকানো যায় না।
মনসুরের আরেকটি কাহিনি শুনুন। একদিন ধ্যানরত অবস্থায় এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে পান মনুসর। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কে?’ জ্যোতির্ময় পুরুষ উত্তর দেন, ‘আনাল হক।’ অর্থাৎ ‘আমিই পরম সত্য’। এরপরই মনসুর নিজেকে ‘আনাল হক’ বা ‘আমি আল্লাহ’ দাবি করেন। ‘আনাল হক’ না বলতে তাঁকে বারণ করা হলো। বারণ শুনলেন না তিনি। ঈমান চলে যাওয়া ও কাফের হওয়ার ভয় দেখিয়েও তাঁকে এই দাবি থেকে ফেরানো গেল না।
মনসুর একদিন গুরু জুনায়েদ বাগদাদির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে গেলেন। দরজায় করাঘাত শুনে ভেতর থেকে জুনায়েদ বললেন, ‘কে?’ উত্তরে মনসুর বললেন, ‘আনাল হক।’ জুনায়েদ দরজা খুলে দেখলেন বাইরে মনসুর দাঁড়িয়ে। শুরু হলো গুরু-শিষ্যের বাকবিতণ্ডা। আনাল হক বলার জন্য মনসুরকে জুনায়েদ সতর্ক করলেন, ‘হয়ত এমন সময় আসছে যখন তুমি কাঠের এক টুকরোয় রক্তের দাগ লাগাবে।’ অর্থাৎ মনসুরকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। উত্তরে মনসুর গুরুর পোষাকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘আর যখন এটা ঘটবে তখন আপনাকে এই জোব্বার বদলে কালো গাউনে নিজেকে ঢাকতে হবে।’
মনসুর হাল্লাজ নিজেকে আল্লাহ দাবির সংবাদটি খলিফা আল মুকতাদিরের কানে পৌঁছল। খলিফা তাঁকে ডেকে এই দাবি প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দিলেন। নইলে তাঁকে শূলে চড়ানোর ভয় দেখালেন। মনসুরের কোনো ভাবান্তর হলো না। আগের মতোই তিনি ক্রমাগত ‘আনাল হক’ বলে যেতে থাকেন। সে সময় মনসুরের পক্ষের লোক যেমন ছিল তেমনি ছিল বিপক্ষের লোকও। আনাল হক বলার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা হলো মামলা। ফেরারি হয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতে থাকেন পথে পথে। তাঁর অনুপস্থিতিতে চলতে থাকে বিচারের কাজ। এক আইনজীবী তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আরেক আইনজীবী দাঁড়ায় পক্ষে। মনসুরের আইনজীবী বলেন যে, আনাল হক মনসুরের মরমি উক্তি। মরমি উক্তি প্রচলিত আইনের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না।
মনসুরের অনুপস্থিতিতে বিচার সম্পন্ন হয়। ৯১৩ সালে তিনি গ্রেফতার হন। কারমাতীয়দের এজেন্ট সাব্যস্ত করে তাঁকে ৯ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আপনারা কি জানেন কারমাতীয় সম্প্রদায় কারা? কারমাতীয়দের বুঝতে হলে আগে শিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে হবে। হযরত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানদের ‘খলিফা’ বা নেতা কে হবে, এ নিয়ে শুরু হয় দ্ব›দ্ব। একটি পক্ষ মত দেয় নেতৃত্ব থাকতে হবে হযরত মুহাম্মদের পরিবারে। এই যুক্তিতে তারা হযরত আলীকে হযরত মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে। আরেক পক্ষ খলিফা মনোনিত করে হযরত আবুবকরকে। যারা হযরত আলীকে সমর্থন করে তারা শিয়া এবং যারা হযরত আবুবকরকে সমর্থন করে তারা সুন্নি নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীকালে শিয়ারা বেশ কটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রধান দুটি উপসম্প্রদায় হচ্ছে ‘ইসনে আশারিয়া’ বা ‘বারোপন্থি শিয়া’ এবং ‘সাবিয়া’ বা ‘সাতপন্থি শিয়া’। বারোপন্থি শিয়ারা বারোজন ইমামের অস্তিত্বে বিশ^াসী। প্রধান ইমাম ছিলেন হযরত আলী। এরপর নবিদৌহিত্র হাসান হোসেন এবং হোসেন থেকে মোহাম্মদ (হযরত মুহাম্মদ নন) পর্যন্ত এসেছেন আরো নয়জন ইমাম।
মোহাম্মদ ইমাম হয়েছিলেন কম বয়সে। ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার পরপরই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর প্রায় সত্তর বছর তাঁর ‘ওয়াকিল’ বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন অন্য চারজন। এই চারজন ওয়াকিলের চতুর্থজন মৃত্যুর সময় তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যাননি। ফলে ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় ইমামের আত্মগোপনের সময়। বারোপন্থি শিয়ারা বিশ^াস করে, ইমাম আজো বেঁচে আছেন। তিনিই ইমাম মেহেদি নামে আবার পৃথিবীতে আসবেন। এখানে আপনাদের জেনে রাখা দরকার যে, সুন্নিরাও ইমাম মেহেদির আবির্ভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে মেহেদি বলে চিহ্নিত করে না।
অপরদিকে সাতপন্থি শিয়াদের মতবাদ বারোপন্থিদের মতোই। কিন্তু দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সপ্তম ইমামকে নিয়ে। ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিকের ছিল দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম ইসমাইল এবং ছোট ছেলের নাম মুসা। বারোপন্থিদের মতে জাফর তাঁর ছোট ছেলে মুসাকে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সাতপন্থিরা ইসমাইলকেই সপ্তম ইমাম বলে ঘোষণা দিয়ে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করে। ইসমাইলের প্রতি অনুগত বলে তাদেরকে ‘ইসমাইলী’ও বলা হয়। ইসমাইলীরা নয়, দশ ও এগারো শতক ধরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এগারো শতকে তারা বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মুসলিম বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের মধ্যে ইসমাইলী চিন্তাধারার প্রভাব ছিল। মেসোপোটেমিয়াতে ‘ইখয়ানুস-সাফা’ ছদ্মনামে দশ শতকে যাঁরা বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন শাখায় পঞ্চাশটিরও বেশি পুস্তিকা রচনা করে প্রচার করেন তাঁরাও ইসমাইলী ছিলেন। আলোক-বিজ্ঞানের পণ্ডিত আল হায়সামও সুন্নি মতবাদের চেয়ে মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকে ইসমাইলী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।
নবম শতকের শেষের দিকে ইসমাইলীরা হামাদান কারমাতের নেতৃত্বে এক ধরনের সামাজিক-ধর্মীয় প্রচারণা শুরু করে। তাঁরই নামানুসারে তারা ‘কারমাতি’ নামে পরিচিতি লাভ করে। ‘কারমাতি’ ছিল গুপ্ত সংগঠন। চাঁদা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে চালানো হতো সংগঠন। কারমাতিয়রা অন্যান্য মুসলমানের প্রতি ছিল বৈরীভাবাপন্ন। তাদের বিরুদ্ধে ছিল নির্যাতন ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ। ৩১৭ হিজরিতে তারা মক্কায় প্রবেশ করে হজরে আসওয়াদ পাথরটিকে তুলে এনে দুই টুকরা করে ফেলে। বারো বছর পর মিশরের তৎকালীন ফাতেমী শাসক কারমাতীয়দের কাছ থেকে পাথরটি উদ্ধার করে জোড়া লাগিয়ে কাবা ঘরে পুনঃস্থাপন করেন। কারমাতীয় আন্দোলনের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয় ফাতেমীয় নামে পরিচিত ইসমাইলীদের আরেকটি শাখা।
কথিত আছে, বন্দিত্বের প্রথম দিন জেলখানা থেকে অদৃশ্য হয়ে যান মনসুর হাল্লাজ। দ্বিতীয় দিন গোটা জেলখানাই অদৃশ্য হয়ে যায়। তৃতীয় দিন জেলকর্মকর্তারা গোটা কারাগারকে আগের মতোই দেখতে পায়। তারা হতবাক হয়ে বলল, হে মনসুর, তুমি এ কোন জাদু দেখালে!
এই ঘটনায় গোটা বাগদাদজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। জুনায়েদ বাগদাদিসহ অনেক ধর্মীয় নেতা ছুটে যান জেলখানায়। ঘটনার ব্যাখ্যা চান মনসুরের কাছে। মনসুর ব্যাখ্যা দিলেন, প্রথম দিন আমি গিয়েছিল খোদার সাক্ষাতে। তাই কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। দ্বিতীয় দিন খোদা এসেছিলেন আমাকে দেখতে। তাঁর নূরের ঝলকানিতে গোটা জেলখানা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।
এই ঘটনার পর জেলখানার রক্ষী ও কয়েদিরা মনসুরের শিষ্য হয়ে যায়। এই জেলখানায় মনসুরকে রাখা হয় এক বছর। বিস্তর মানুষ প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। এই সংবাদ জেনে কেউ মনসুরের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না বলে আদেশ জারি করেন খলিফা। এসময় সুফি ইবনে আতা বার্তাবাহকের মাধ্যমে মনসুরের কাছে খবর পাঠালেন যে, মনসুর যদি প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্মবিরোধী বক্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের ভুল স্বীকার করে, তাহলে খলিফা হয়ত তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। বার্তাবাহকে মনসুর বললেন, ‘যিনি এই কথা বলে তোমাকে পাঠিয়েছেন তাকে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বলো।’ একথা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইবনে আতা।
খলিফার নির্দেশের পরও জেলখানায় দর্শনার্থীদের ঠেকানো যাচ্ছিল না। অগত্যা খলিফার নির্দেশে মনসুরকে অন্য কারাগারে সরিয়ে নেওয়া হয়। কথিত আছে, ওই কারাগারে ছিল তিন শ বন্দি। এক রাতে মনসুর তাদেরকে বললেন, তোমরা কি মুক্তি চাও? বন্দিরা বলল, আমাদের মুক্ত করার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, তবে তুমি নিজেই মুক্ত হচ্ছ না কেন? আর তখন গরাদের শিকগুলোর দিকে তাকালেন মনসুর। সঙ্গে সঙ্গে সব কটি দরজা খুলে গেল। পালিয়ে গেল সব বন্দি। পলায়নরত এক বন্দি মনসুরকে বলল, তুমি পালাচ্ছ না কেন? মনসুর বললেন, আমি খোদার প্রেমের পাগল, মুক্তির পাগল নই।
উচ্চ আদালতে মনসুরের বিচার চলছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পক্ষে কোনো স্বাক্ষী ছিল না বলে ১০১ জন আলেমের সম্মতি নেওয়া হচ্ছিল। জুনায়েদ বাগদাদিই প্রথম মনসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়ার কাগজে স্বাক্ষর করেন। ১০০ জন আলেমের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা গেল, কিন্তু একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তিন শ বন্দিকে মুক্ত করার অপরাধে বাগদাদের কাজি যখন মনসুরকে প্রকাশ্য তিন শ বেত্রাঘাত করার আদেশ দেন, তখন মনসুর নিজেই ১০১তম স্বাক্ষী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। খলিফার অনুমতির পর তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়।
মনসুর হাল্লাজের শাস্তিকে দৃষ্টান্তমূলক করার দাবি ছিল। আর তাই মৃত্যুদণ্ডের আগে তাঁকে এক উম্মুক্ত প্রান্তরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। শরিয়ত মোতাবেক লোকজন তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। তাতে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না, নীরবে সয়ে যেতেন। আর কেবলই উচ্চারণ করতেন আনাল হক ধ্বনি। মনসুরের বন্ধু শিবলি এসময় তাঁর দিকে একটি গোলাপ ছুঁড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনসুর চিৎকার করে ওঠেন। লোকজন এই চিৎকারের কারণ জানতে চাইলে মনসুর বলেন, সবাই আমাকে না চিনে না বুঝে পাথর মারছে। কিন্তু শিবলি আমাকে চেনে, জানে। আমি আসলে কী বলতে চাই সে তা বোঝে। জেনে-বুঝে সে আমাকে গোলাপ ছুঁড়েছে। আমি আঘাত পেয়েছি।
দীর্ঘক্ষণ ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রাখার পরও মনসুরের মৃত্যু হলো না। বিচারকের নির্দেশে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে নামানো হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় হাত-পা কেটে দেওয়ার জন্য, যাতে রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। তাই করা হলো। রক্তক্ষরণে তাঁর শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তবু তিনি মরলেন না। তখনো তিনি নিরুদ্বেগ। শান্তস্বরে উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন আনাল হক ধ্বনি। এবার তাঁর নাক, কান ও জিব কেটে ফেলা হয়। তারপর যখন তাঁর চোখ উপড়ে ফেলা হয় তখন সমবেত জনতা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। তারপর কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তাঁর শরীরটি। টুকরোগুলো দর্শনাথীদের জন্য ছড়িয়ে রাখা হয়, যাতে এই ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। পরদিন সকালে মানুষেরা আবিষ্কার করল মনসুরের দেহের খণ্ডিত টুকরোগুলোতে প্রাণ রয়েছে এবং তা থেকে অবিরত আনাল হক ধ্বনিত হচ্ছে। বিচারক ও একদল আলেম দ্রুত ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে। এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন তারা। পরামর্শের জন্যে ছুটে গেলেন জুনায়েদ বাগদাদির কাছে।
সব শুনে বাগদাদি বললেন, আল্লার সাথে মনসুর হাল্লাজের সাক্ষাৎ লাভ হয়ে গেছে। নিজের ভেতর যখন তিনি আল্লাহকে দেখেছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলেন, মান আনতা? অর্থাৎ তুমি কে? আল্লাহ বলেছিলেন, আনাল হক। অর্থাৎ আমি আল্লাহ। আর সেই উচ্চারণই মনসুরের দেহ প্রতিধ্বনিত করছে মাত্র।
এই ঘটনা খলিফাকে জানানোর পর বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। তৎক্ষণাৎ মনসুরের শরীরের টুকরোগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাঁর আশংঙ্কা ছিল জনতার আবেগ না পরে আবার ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে বসে!
খলিফার আদেশে মনসুরের খণ্ডিত টুকরোলোতে তেল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলা হলো। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল পরদিন, যখন তাঁর ছাইভষ্ম টাইগ্রিস নদীতে ফেলা হয়। ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল নদীর পানি। ধেয়ে আসতে লাগল নগরীর দিকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল নগরবাসী। তখন সামেরী নামে মনসুরের এক শিষ্য দৌড়ে গিয়ে মনসুরের ব্যবহৃত একটি জোব্বা এনে ছুড়ে দেয় পানিতে। সামেরী বলেছিল, মৃত্যুর চল্লিশ দিন আগে মনসুর তাকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে যেন জোব্বাটি ছুড়ে দেওয়া হয়।
মনসুর হাল্লাজ বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে কিতাব আল-তাওয়াসিন। এই গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। সম্ভবত তাঁর কোনো শিষ্য সেটিকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। এগারটি অধ্যায়ের গ্রন্থটি অতীন্দ্রিবাদ বা গুপ্তজ্ঞান অর্জনের দিশারী। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক রায়হান রাইন। সংবেদ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। আপনারা চাইলে সংগ্রহ করতে পারেন। গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়ে আল্লাহ ও ইবলিসের সংক্ষিপ্ত সংলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে।
আল্লাহ যখন আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন, সব ফেরেশতা সেজদা করে, করে না শুধু ইবলিস। সে কেন সেজদা করল না? মনসুর হাল্লাজ ব্যাখ্যা করেন, ইবলিস আদমকে সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই আল্লাহকে জেনেছে, লক্ষাধিক বছর তাঁর উপাসনা করেছে, তাঁকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে সেজদা করেছে। সে এখন কী করে এমন কাউকে সেজদা করে, যে কিনা আল্লাহর চেয়ে নিকৃষ্ট মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? এই কারণেই সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। তার এই অস্বীকৃতি বিয়োগান্তকভাবে আল্লাহকেই অস্বীকারের পর্যায়ে পড়ে যায়। মনসুর হাল্লাজ ইবলিসকে খাঁটি একত্ববাদী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন কিতাব আল-তাওয়াসিন গ্রন্থে।
সুফি জুনায়েদ বাগদাদি ছিলেন একাধারে গূঢ়ততত্ত্বে নিষ্ঠাবান অনুসারী ও ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি আস্থাবান। কিন্তু মনসুর সম্পূর্ণ তাঁর বিপরীত। মনসুরের মতে, একজন একনিষ্ঠ সুফির জন্য প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান মানার প্রয়োজন নেই। সুফি বায়েজিদ বোস্তামি ব্যক্তিসত্তার বিনাশকে (ফানা) ঐশীসত্তায় মেলানোর কথা বলেছেন। কিন্তু মনসুর হাল্লাজ সেই বিনাশ হওয়া থেকে ফের উত্থিত হওয়ার (বাকা) কথা বলেছেন। অর্থাৎ ঐশীসত্তায় বিলীন হয়ে আবার বেঁচে ওঠা। এ অবস্থায় মনসুরকে দেখা মানেই আল্লাহকে দেখা, আর আল্লাহকে দেখা মানেই মনসুরকে দেখা।
মনসুর হল্লাজের মৃত্যুর কিছুদিন পর আবু নাসর আব্দুল্লাহ বিন আলী আল-সাররাজ আল-তুসি তাঁর কিতাব আল-লুমায় লেখেন :
‘সুফি চিন্তার মানুষেরা গেছে চলে
সুফিবাদ এখন শতচ্ছিন্ন এক জামা ছাড়া কিছু নয়
সেই বিশেষ জ্ঞান গেছে চলে
কোন আলোকিত হৃদয় বাকি নেই।’
————————————————————–
বই : ‘মুসলিম মনন ও দর্শন : অগ্রনায়কেরা’
লেখক : স্বকৃত নোমান
রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।